তারুণ্যের স্বদেশচিন্তা ও রাজনীতির নতুন মেরুকরণ

রুকাইয়া তাসনিম তন্বী: বিগত দশকে বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে বড় পরিবর্তনটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হলো তারুণ্যের রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ এবং নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ পরিবর্তন নিছক একটি প্রজন্মগত রূপান্তর নয়, বরং এটি একটি কাঠামোগত ও আদর্শিক রূপান্তর, যা রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্কের নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছে।

১. রাজনৈতিক সচেতনতার নতুন তরঙ্গ: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, যে কোনো সমাজে রাজনৈতিক মেরুকরণ তখনই ঘটে যখন নাগরিকরা বিদ্যমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে প্রশ্ন করে এবং বিকল্প আদর্শ খোঁজে। এই মুহূর্তে তরুণ প্রজন্ম ঠিক সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষার অধিকার, তথ্যের স্বাধীনতা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা, এসব ইস্যুতে তারুণ্যের সক্রিয়তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় issue-based politics বা ‘ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি’-এর পরিচায়ক।


২. নতুন গণতান্ত্রিক চর্চার অভিমুখ: তারুণ্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি নতুন রূপ দেখা যাচ্ছে, যেখানে তারা শুধু ভোটদানে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং তারা অংশ নিচ্ছে রাজনৈতিক বিতর্ক, সামাজিক আন্দোলন ও ডিজিটাল ক্যাম্পেইনে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় deliberative democracy. অর্থাৎ যুক্তিভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র। এই প্রক্রিয়ায় তারা ‘রাষ্ট্র বনাম নাগরিক’ নয় বরং ‘রাষ্ট্রের ভেতরেই নাগরিক শক্তি’, এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।
৩. রাজনৈতিক মেরুকরণের রূপান্তর: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মেরুকরণ দীর্ঘদিন ধরে মূলত দলীয় বিভক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন একটি নতুন মেরুকরণ লক্ষ করা যাচ্ছে, যা দলীয় পরিচয়ের চেয়ে নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্ভাবনাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।
নতুন প্রজন্ম দলকে প্রশ্ন করছে, নেতাকে নয়; তারা আদর্শ খোঁজে, কুল্ট নয়। এটাই হচ্ছে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের বৈশিষ্ট্য, যেখানে তারুণ্যের চিন্তা-ভাবনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় post-ideological but ethical politics. অর্থাৎ আদর্শ-উত্তর কিন্তু নৈতিকতানির্ভর রাজনীতির দিকে এগোচ্ছে।
৪. ডিজিটাল নাগরিকত্ব ও তথ্যের যুদ্ধ: তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে তরুণরা এখন রাষ্ট্রের ওপরে এক নতুন রকমের নজরদারি চালাচ্ছে, যা এক ধরনের watchdog citizenship। তারা রাষ্ট্রীয় নীতির বিশ্লেষণ করে, ভুল তুলে ধরে এবং ন্যায়ের দাবি তোলে। আবার একই সঙ্গে, এই তথ্যযুদ্ধই কখনো কখনো বিভ্রান্তি ও বিভাজনের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরি হলো information asymmetry, যেখানে তথ্যের ভারসাম্যহীনতা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। তরুণদের মধ্যে এই সচেতনতা জন্ম নিচ্ছে, তারা শুধুই তথ্যগ্রহীতা নয়, বরং তথ্য নির্মাতা।
ভবিষ্যতের দিশা: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল কথাই হলো রাষ্ট্র কেবল শাসনের যন্ত্র নয়, বরং তা একটি চুক্তিভিত্তিক সমন্বয় (social contract)। তরুণ প্রজন্ম এখন এই চুক্তিকে নতুনভাবে লিখতে চায়। তারা চায় এক ধরনের অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র, যেখানে তাদের কণ্ঠস্বর শুধু শোনা হবে না, গ্রহণও করা হবে।
এই চেতনা থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন সংগঠন, নতুন আন্দোলন, নতুন সংলাপ, যা ধীরে ধীরে একটি বিকল্প রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলছে।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেখায় যে কোনও সমাজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার চিন্তাশীল নাগরিকদের উপর। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম যদি এই ভাবনাগুলোর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতির নতুন মেরুকরণ শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, সম্ভবও বটে।
রাষ্ট্র বদলায় শুধু ক্ষমতার পালাবদলে নয়, চিন্তার পরিবর্তনে। আর সেই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি, তারুণ্য।
একটি পরিবর্তনশীল সময়ের পটভূমি থেকে বিশ্লেষণসময়ের পালাবদলে সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপ যেমন বদলায়, তেমনি বদলায় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন একটি নতুন চালচিত্র তৈরি হচ্ছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তারুণ্য।
তরুণ প্রজন্মের স্বদেশচিন্তা এখন আর আগের মতো সরল আবেগনির্ভর নয়। এটি এখন বিশ্লেষণমূলক, জিজ্ঞাসুনির্ভর এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে। ফলে রাজনীতির চিরাচরিত মেরুকরণে একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে, একটি তৃতীয় মেরু তৈরি হচ্ছে, যেটি আদর্শিক, নৈতিক ও অংশগ্রহণমূলক চেতনায় ভরপুর।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতির ধারাও বদলে যায়। তবে আজকের বিশ্বে, এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ চালক হচ্ছে তারুণ্য। প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন এবং তথ্যপ্রবাহের অগ্রগতির ফলে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল এবং সচেতন। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এই প্রজন্ম এখন আর নিছক দর্শক নয়; বরং তারা সক্রিয়, প্রশ্নবিদ্ধ ও বিকল্পমুখী।
নতুন স্বদেশচিন্তা: বাংলাদেশের তরুণরা এখন রাষ্ট্রকে দেখে প্রশ্ন নিয়ে, কে কেমন শাসন করছে, কারা উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছে, কোথায় বৈষম্য বাড়ছে? এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানে, কিন্তু তারা জানতে চায়, কেন স্বাধীনতার এত বছর পরও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়নি সবার জন্য?
তারা দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে অনলাইন অ্যাক্টিভিজম, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ বা দুর্নীতিবিরোধী আওয়াজ তুলে। তাদের স্বদেশচিন্তা এখন দায়বদ্ধতা, জবাবদিহি ও সামাজিক ন্যায়ের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। তরুণরা এখন চায়, নেতার চেয়ে নীতির জয় হোক। রাজনৈতিক লড়াই হোক আদর্শের ভিত্তিতে, পেশিশক্তি বা পরিচয় নয়।
স্বদেশচিন্তার রূপান্তর: স্বদেশচিন্তা মানে শুধু দেশপ্রেম বা আবেগ নয়, এখন এটি একেবারে বাস্তবভিত্তিক, বিশ্লেষণধর্মী ও অন্তর্দৃষ্টি-সমৃদ্ধ একটি চর্চা। তরুণরা এখন আর শুধু গর্বের ইতিহাস জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা জানতে চায়, সেই ইতিহাস থেকে তারা কী শিখবে এবং কীভাবে বর্তমানকে বদলাবে। তারা দেখে, একদিকে উন্নয়ন, অন্যদিকে বৈষম্য; একদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ, অন্যদিকে চাকরির বাজারে অনিশ্চয়তা। এই দ্বৈততা তাদের স্বদেশচিন্তায় এক ধরনের জবাবদিহির চেতনা সৃষ্টি করেছে।
তরুণরা এখন আর কেবল রাজনৈতিক দলের ব্যানার দেখে ভোট দেয় না, তারা খোঁজে কর্মপরিকল্পনা, আদর্শিক স্থিতি এবং নেতৃত্বের সততা। এই পরিবর্তন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় একটি ‘সংবেদনশীল রাজনৈতিক নাগরিকত্ব’ গঠনের সূচনা।
রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ: বাংলাদেশের রাজনৈতিক মেরুকরণ দীর্ঘদিন ধরে দুই মূলধারায় বিভক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান তরুণ প্রজন্ম এসব দ্বন্দ্বে আগ্রহ হারাচ্ছে। তারা চায় তৃতীয় ধরনের রাজনীতি, যেখানে ব্যক্তি নয়, প্রতিষ্ঠান মুখ্য; প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ।
এই ‘নতুন মেরুকরণ’ কোনো তৃতীয় দল নয়, বরং তৃতীয় ধরনের রাজনৈতিক দর্শন, যেখানে তরুণরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে চায়, কিন্তু পুরনো রাজনীতির অনৈতিক খেলায় অংশ নিতে রাজি নয়। তরুণদের এই অংশগ্রহণ কখনো দেখা যায় ক্যাম্পাসে ছাত্র আন্দোলনে, কখনো অনলাইন প্রচারণায়, আবার কখনো স্থানীয় সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে। এই জাগরণ রাজনীতির জন্য একটি সতর্ক সংকেত, তরুণরা আর নীরব দর্শক নয়।
শিক্ষিত ও সচেতন তরুণদের একটি বড় অংশ এখনো রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িত না হলেও তারা সামাজিক আন্দোলন, অনলাইন অ্যাক্টিভিজম বা স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। তারা চাইছে দুর্নীতিমুক্ত, অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ একটি শাসনব্যবস্থা।
রাজনৈতিক বিতর্কে তারা যুক্তির চর্চা চায়, ব্যক্তির পূজা নয়। এই মেরুকরণ অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত এবং এটি মূলধারার রাজনীতিকে চাপে ফেলছে। তরুণদের এই চেতনা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এখন একটি চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার মিশেল। তারুণ্যের এই জাগরণ অমূল্য সম্পদ, তবে তা যাতে হতাশায় রূপ না নেয়, সে দায়িত্ব কেবল তরুণদের নয়, রাষ্ট্র ও সমাজেরও। শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে সমালোচনামূলক চিন্তা ও নৈতিক নেতৃত্ব তৈরির উপযোগী।
রাজনৈতিক দলগুলোকে দরকার সংস্কার, তরুণদের জন্য বাস্তব অংশগ্রহণের সুযোগ, কেবল মুখের বুলি নয়। সামাজিক মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেন গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতার ভিত গড়ে তোলে, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি। বাংলাদেশের তারুণ্যের স্বদেশচিন্তা এখন আর আবেগে ভাসা নয়, এটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক বোধের প্রতিফলন। আর এই বোধই রাজনীতিতে একটি নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখানে তারুণ্য শুধু পরিবর্তনের আশা নয়, বরং পরিবর্তনের নকশাকার। এই নকশায় যদি অংশ নেয় রাষ্ট্র, দল ও সমাজ; তবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ শুধু উন্নয়নশীল নয়, হবে ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি রাষ্ট্র।
লেখক: শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।















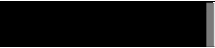
Recent comments
Latest Comments section by users
No comment available